সাজ্জাদ বিপ্লব
কবি। সম্পাদক। গবেষক। প্রকাশক। সংগঠক। লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রাহক। জন্মশহর বগুড়ায় গড়ে তুলেছেন বই ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কেন্দ্র : পুণ্ড্রনগর লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি।

কবি। সম্পাদক। গবেষক। প্রকাশক। সংগঠক। লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রাহক। জন্মশহর বগুড়ায় গড়ে তুলেছেন বই ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কেন্দ্র : পুণ্ড্রনগর লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি।

মোরশেদ শফিউল হাসান
আবু করিম বিশ্বাস করে কবিত্বশক্তি আল্লাহর দান, ইচ্ছা করলেই কেউ কবি হতে পারে না। সাম্প্রতিককালে সে দু-এক জায়গায় লিখেছেও এ-কথা। জানি না, জীবনানন্দের ‘সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি’র মতো তার এই উক্তিটিও কালে প্রবাদপ্রতিমতা অর্জন করবে কি না । আপাতত আমি শুধু জানাতে চাই, করিমের এই কথাটাতে আমারও বিশ্বাস শতকরা একশো ভাগ। চাইলে বা চেষ্টা করলেই সবাই কবি হতে পারে না। অনেকেই আমরা চেয়েছিলাম, কেউ কেউ এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে একজনই কেবল কবি হতে পেরেছে, সে আবু করিম। পরবর্তীকালে আবু করিম হয়তো আরও অনেক কিছু হতে চেয়েছে, হয়েছে। সাংবাদিক, রাজনৈতিক সংগঠক, আমলা। কিন্তু, আমি যদি বুঝতে ভুল না করে থাকি, আমাদের সে কৈশোর ও তারুণ্যের দিনগুলোতে সে এক ও একমাত্র কবিই হতে চেয়েছিল। আর এর জন্য যথেষ্ট মূল্য তাকে দিতে হয়েছে, অনেক লড়াই লড়তে হয়েছে। আমার গর্ব, সে-লড়াইয়ে আমরা ছিলাম সহযোদ্ধা। যেমন কিভাবে যেন আমাদের দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল, কবি-লেখক হতে হলে অন্যান্য সহপাঠীদের মতো আমাদের বিজ্ঞান পড়লে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখলে চলবে না; একাডেমিক পড়ালেখা যদি একান্ত করতেই হয় তবে সাহিত্য নিয়েই পড়তে হবে। বিজ্ঞান ছেড়ে আমরা তাই প্রথমে মানবিক শাখায়, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হলাম বাংলা বিভাগে। আমাদের আগেপরে অবশ্য এ-কম্মটি আরও অনেকেই করেছেন। কিন্তু যত সহজভাবে আমি কথাটা বললাম, বিশেষ করে আমাদের মতো প্রায় নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দুটি সন্তানের পক্ষে, তা-ও আবার মোটামুটি ভালো পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে, সেদিন কাজটা করা মোটেও তত সহজ ছিল না। পারিবারিক-পারিপার্শ্বিক অনেক বাধা, নানা অপ্রিয় পরিস্থিতির মোকাবেলা করে আমাদের সিদ্ধান্তটা কার্যকর করতে হয়েছে। দিনের পর দিন আমাদের কেটেছে এ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, জল্পনা-কল্পনা ও ‘রণকৌশল’ নির্ধারণের উত্তেজনার মধ্যে। উনসত্তরের অগ্নিক্ষরা দিনগুলোতে আমরা রাজপথে একসঙ্গে মিছিল করেছি, পুলিশের টিয়ার গ্যাস খেয়েছি; কিন্তু সে-সময়ই ঘরে-বাইরে পাশাপাশি এই যে-আরেকটি লড়াই আমাদের লড়তে হয়েছে তার মূল্য বা গুরুত্বও আমাদের জন্য বেশি বৈ কম ছিল না।
১৯৬৪ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে আমি আবু করিমকে আমার সহপাঠী হিসেবে পাই। সেই থেকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পর্যন্ত সে ছিল আমার সহপাঠী। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে দিবা শাখায় আমরা ছিলাম বি-সেকশনের ছাত্র। আমাদের স্কুলে বি-সেকশনটিকেই ভালো ছাত্রদের ক্লাশ বলে গণ্য করা হত। পলোগ্রাউন্ড, টাইগার পাশ, আমবাগান এসব রেলওয়ে এলাকা থেকে আমরা অনেকে রেল লাইন ধরে এক সাথে স্কুলে যাওয়া-আসা করতাম (সে-সময় চাটগাঁ শহরের প্রায় অর্ধেকটাই জুড়ে ছিল মনে হয় বিভিন্ন রেলওয়ে আবাসিক এলাকা; শহরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন ও ক্রীড়াঙ্গনকে বলতে গেলে তারাই প্রাণচঞ্চল রাখত)। কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হবার পরও প্রথমদিকে আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল আমার পুরনো প্রাইমারি স্কুলের সহপাঠী বা রেল কলোনীর বাসিন্দা। আবু করিমের বাবাও যদিও রেলওয়েতেই চাকুরি করতেন (অনেক পরে আমি তা জেনেছি) তিনি কিন্তু, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের গ্রামের বাড়িতে রেখে, কেবল আবু করিমকে নিয়ে মাদারবাড়ি বা মোগলটুলি এলাকায় কোনো মেসবাড়িতে থাকতেন। আমাদের এক রকম আধা-শহুরে উন্নাসিকতা বা কলোনী জীবনের সঙ্কীর্ণতার (যেভাবেই আজ বিষয়টাকে ব্যাখ্য করি না কেন) বেড়া ডিঙ্গিয়ে, উপরন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার অমিশুক স্বভাব নিয়ে, সদ্য গ্রাম বা মফস্বল থেকে আসা আবু করিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াটা সুতরাং সহজ বা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। হ্যাঁ, হতে সময় লেগেছিল। তাছাড়া আবু করিমের মধ্যেও তখন কেমন যেন একটা সঙ্কুচিত ভাব কাজ করত। আমাদের সে-সময়ের সহপাঠীরা অনেকেই সেটা স্মরণ করতে পারবেন। হয়তো তারপরও ক্লাশের কারো কারো সঙ্গে তার অল্পদিনেই বন্ধুত্ব হয়েছিল, তবে তাঁদের কেউ আমার বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ ছিল না। মোটকথা আবু করিমের যদি লেখালেখির অভ্যাস না থাকত এবং ওই বয়সেই যদি আমার মধ্যেও কিঞ্চিৎ সাহিত্যানুরাগ ও পাঠাভ্যাস না জন্মাত তাহলে কে জানে হয়তো কোনোদিনই তার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হত না।
আরও কিছু বিষয়ের মতো আমাদের স্কুলে জোহরের নামাজ পড়াটা ছিল বাধ্যতামূলক। যারা নামাজ পড়েনি প্রতিদিন ক্লাশ-ক্যাপ্টেন হিসেবে আমাকে তাদের নামের তালিকা তৈরি করতে হত। টিফিন পিরিয়ডের পর ধর্মশিক্ষার ক্লাশে হেডমৌলবি সাহেব এসে প্রথমেই যে-কাজটি করতেন তা হল, সে তালিকা ধরে, যারা নামাজ পড়েনি তাদের শায়েস্তা করা। এই প্রক্রিয়ায় আবু করিমও হয়তো কখনো কখনো তাঁর বেত্রাঘাতের শিকার হয়ে থাকবে। করিম তার ‘নৌকোজীবন’ উপন্যাসে সম্ভবত সে-স্মৃতিটিকেই তুলে এনেছে এভাবে : “ক্লাস-ক্যাপ্টেন মোরশেদের ক্লাসের শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা ছাড়াও একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিলো। সে দুপুর বেলা টিফিনের সময় স্কুল মসজিদে নামাজ পড়ার হাজিরা দেখতো। যারা যারা নামাজ পড়তো না তাদের নাম সে টুকে রাখতো এবং পরে হেড মৌলভীর কাছে নালিশ করতো। হেড মৌলভীর ক্লাস ছিল টিফিন আওয়ারের পরে। তিনি সেই লিষ্টি ধরে ধরে প্রত্যেককে দু’ঘা করে বেত মারতেন। … মোরশেদ ঠিকই আমার নামে নালিশ জানাতো আর আমি মার খেতাম। মার খেতে খুব কষ্ট হতো আমার।” উপন্যাস তো উপন্যাসই। বস্তুত আবু করিম তার শিল্পী মনের মাধুরী মিশিযে অনেক ‘ইতিহাসের’ই সেখানে পুনর্গঠন করেছে। উপন্যাসে উল্লেখিত ‘মোরশেদ’ চরিত্রটি যে আমিই একথাই বা কেন ভাবব? তারপরও, আজ ও আগামীদিনের আবু করিমের ভক্ত পাঠক ও অনুরাগীদের দরবারে আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি শুধু নিবেদন করতে চাই, তাঁদের প্রিয় কবির এই প্রহৃত হবার ব্যাপারে আমার সত্যিসত্যি কোনো সচেতন ভূমিকা ছিল না (না, করিমও তেমন কথা লেখেনি)। কারণ তাঁর প্রতিভা আবিষ্কার তো দূরের কথা, আমি আসলে তখনও তাকে ভালোভাবে চিনতাম না। বর্তমানে আবু করিম একজন পাক্কা নামাজি, আমাদের সে মৌলভি স্যার কিংবা তাঁর আত্মা (জানি না তিনি জীবিত আছেন কি না) একথা জানতে পেলে নিশ্চয়ই যার পর নেই খুশি হবেন।
১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। আমরা তখন ৭ম শ্রেণীর ছাত্র। এ-সময় আমাদের ক্লাশ টিচার যিনি ছিলেন তাঁর নাম সিদ্দিকুল্লাহ। যুদ্ধের উত্তেজনায় তখন সবাই যাকে বলে টগবগ করে ফুটছে। আমরা বাচ্চা ছেলেরাও তার থেকে বাদ ছিলাম না। মনে আছে এ-সময় আমরা একদিন স্কুল থেকে মিছিল করে লালদীঘির মাঠ পর্যন্ত গেলাম, বড় ভাইরা সেখানে বক্তৃতা করলেন, তারপর আবার মিছিল করে নারা লাগাতে লাগাতে সবাই স্কুলে ফিরে এলাম। তো যে-কথা বলার জন্য এ-প্রসঙ্গের অবতারণা তাতে ফিরে আসি। যুদ্ধের সর্বশেষ ‘অগ্রগতি’ – পাকিস্তান বাহিনী কোন্ সেক্টরে কতদূর এগিয়ে গেছে, তারা ভারতীয় এলাকার কতটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে, কটি ভারতীয় ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে, কটি ভারতীয় বিমান ভূপাতিত করেছে – এসব খবর জানতে তো আমাদের দারুণ উৎসাহ! সিদ্দিকুল্লাহ স্যারও প্রতিদিন ক্লাশে এসে এসব গল্পই শোনান। তা তিনিই একদিন বললেন, যুদ্ধের খবরাখবর ও সেই সঙ্গে কিছু দেশপ্রেমমূলক লেখাটেখা নিয়ে আমরা ক্লাশেই একটা দেয়াল পত্রিকা বের করি না কেন। সে পত্রিকা সম্পাদনার প্রধান ভারটা পড়ল আমার ওপর। সহপাঠীদের আরও একজন কি দুজন এ কাজে আমার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে আবু করিম তাদের মধ্যে ছিল কিনা আজ এতদিন পর সেকথা মনে করতে পারছি না (খুব সম্ভব ছিল)। তবে যা খুব ভালোভাবে মনে আছে তা হল, এ-সময় প্রায় প্রতিদিনই সে দেয়ালপত্রিকার জন্য স্বরচিত কবিতা-ছড়া ইত্যাদিসহ একতাড়া লেখা নিয়ে হাজির হত। এ-ও মনে আছে, তার একটি লেখা আমি একদিন দেয়ালপত্রে দিতে রাজি না হওয়ায় সে আমার বিরুদ্ধে সিদ্দিকুল্লাহ স্যারের কাছে নালিশ করেছিল (করিম, তোমার কি মনে আছে?)। আমি আমার তরফে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম। শেষে মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। তো এভাবেই সপ্তম শ্রেণীতে পৌঁছে আমি ও আমাদের অন্যান্য সহপাঠীরা ক্লাশের দ্বিতীয় ‘সাহিত্যিক-ছাত্র’টির অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হই।
হাই স্কুল জীবনের গোড়ায় নতুন যাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল অহিদুল আনোয়ার। ওই বয়সেই নানা বিষয়ে ছিল তার জানাশোনা ও কৌতূহল। দেশ-বিদেশের রাজনীতিসহ অনেক খবরাখবর সে রাখত। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ত, রেডিও শুনত। ফলে ‘কমন ইন্টারেস্ট’ থেকে খুব সহজেই আমাদের বন্ধুত্বটা গাঢ় হয়ে ওঠে। স্কুল শুরুর আগে, টিফিন পিরিয়ডে এমনকি খেলাধুলার ঘণ্টায় সবাই যখন মাঠে নামত, তখন আমরা সদ্য-পড়া কোনো বই, আকাশবাণীতে আগের দিন শোনা কোনো প্রিয় গান বা নাটক কিংবা দেশ-বিদেশের কোনো ঘটনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। আরও দু-চারজন সহপাঠীও কখনো কখনো আমাদের সঙ্গে জুটে যেত। তবে আবু করিম কখনো আমাদের সে আড্ডায় যোগ দিয়েছে বলে মনে পড়ে না। সম্ভবত সে-সময় খেলাধুলা বা এ ধরনের বিষয়ই তাকে বেশি টানত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে মাস্টার্স করে অহিদুল আনোয়ার পরে আবু করিমের সঙ্গে একই ব্যাচে প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দেয়। দূর প্রবাসে পরিজনবিচ্ছিন্ন অবস্থায় অকালে আমাদের এই বন্ধুটির মৃত্যু হয়েছে। তার স্মৃতিচারণ করে আবু করিম তাদের ক্যাডার সমিতির মুখপত্রে একটি লেখাও লিখেছে বলে জানি। তো আমাদের সে রসিক বন্ধুটি কী কারণে জানি না, আবু করিমকে খুব একটা পছন্দ করতে পারত না। গোড়া থেকেই করিমের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাকে সে ভালোভাবে নিতে পারেনি। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না, ‘নোয়াখাল্যা’ করিমের সঙ্গে কী করে আমার বন্ধুত্ব হয়। এমনকি করিম যে কবিতা লেখে সেটাও তার কাছে ছিল একটা আশ্চর্য, প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অন্তত তার কথাবার্তায় এরকমই ভাব প্রকাশ পেত। পরবর্তীতে আবু করিমের সঙ্গে আমার যতই ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে ততই অহিদের সঙ্গে আমার এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়। হয়তো সেটাই একমাত্র কারণ নয়, তবে প্রধান কারণ ছিল সেটাই।
ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কলেজিয়েট স্কুলে প্রথমে ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া ও মেনন গ্রুপ যৌথভাবে) নির্বাচনী দল ‘অগ্রগামী’ ও পরে ১৯৬৮-৬৯ সালে সরাসরি ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) শাখা গঠনের ব্যাপারে যে দু-চারজনকে আমি পাশে পেয়েছিলাম তার মধ্যে করিম ছিল অন্যতম। সেদিন অনেক বাধাবিপত্তি উজিয়ে, দারুণ ঝুঁকি নিয়ে, আমাদেরকে কাজটা করতে হয়েছিল। বাধাটা কেবল স্কুল কর্তৃপক্ষের দিক থেকেই ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের তরফ থেকেও আমরা সেদিন প্রবল হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলাম। তবে যতদূর মনে পড়ে ওই পর্যায়ে রাজনীতি ছাড়া অন্যান্য বিষয়েই করিমের আগ্রহ ছিল বেশি । পরে আমরা চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ১৯৭০এ আমাদের দু বন্ধুর মধ্যে একজনকে ছাত্র ইউনিয়ন কলেজ শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক (আমি অবশ্য আগেই শহর শাখার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলাম) ও করিমকে ছাত্র ইউনিয়নেরই নির্বাচনী দল ইউএসপিপি-র সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক করা হয়। এ সময় থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে সংগঠনের দৈনন্দিন কার্যক্রমে অংশ নিয়েছি। সে-সময়ে কলেজ ছুটির পর আমাদের নিয়মিত রুটিন ছিল প্রথমে পাবলিক লাইব্রেরি ও তারপর সেখান থেকে ছাত্র ইউনিয়নের জেলা অফিসে যাওয়া। সেখানে বিভিন্ন সভা-অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে যথেষ্ট রাত করে বাড়ি ফেরা। এ-সময়ই আমরা আবার চট্টগ্রাম কলেজে ‘আমরা সূর্যমুখী’ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও উক্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে ‘অতন্দ্র’ নামে একটি সংকলন প্রকাশ করি। সে-সম্পর্কে দু’একটি কথা আবু করিম ও আমি অন্যত্র লিখেছি।
সবাই হয়তো জানে না, আবু করিমের প্রথম দিকের বেশকিছু কবিতা তাঁর পিতৃদত্ত নামেই ছাপা হয়। আ. ত. ম. ফজলুল করিমের আবু করিমে পরিণত হওয়ার ঘটনাটিরও আমি সাক্ষী। সেদিনকার কথাটা আমার এখনও প্রায় স্পষ্টই মনে আছে। ছাত্র ইউনিয়ন জেলা শাখার একুশের সংকলন ‘পদাতিক’-এর জন্য মাহবুব ভাই (বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক) লেখা দিতে বলেছেন। আমরা দু’ বন্ধু যার যার কবিতা নিয়ে একসঙ্গে ছাত্র ইউনিয়নের তখনকার নাজির আহমদ চৌধুরী সড়কস্থ অফিসে রওনা হয়েছি। করিম কিছুদিন থেকেই তাঁর দীর্ঘ নামটি বদল বা ছেঁটে ছোট করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছিল, কিন্তু ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। সেদিনও হাঁটতে হাঁটতেই এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ কাটাপাহাড় লেনের কাছে এসে সে তার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলল। পকেট বা হাতের প্যাকেট (ঠিক মনে নেই) থেকে লেখাটা বের করেই আমার পিঠের ওপর রেখে লিখে ফেলল ‘আবু করিম’। খুব সম্ভব ‘দুটি ট্রিওলেট’ নামে ‘পদাতিক’-এ প্রকাশিত সে-লেখাই ছিল আবু করিম নামে ছাপা তার প্রথম রচনা। সেটা ১৯৬৯ সালের কথা। ট্রিওলেট দুটির একটির শুরুটা ছিল এরকম : ‘গণমিছিলের পথ বেয়ে ওরা আসে, / ওরা অগ্নিযুগের বন্দি সূর্যসেনা/জ্বালা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ওরা হাসে’ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে করিমকে তার এই নামের অর্থ নিয়ে কোথাও কোথাও প্রশ্ন বা বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সে-রকম একটি-দুটি ঘটনারও আমি যাকে বলে প্রত্যক্ষদর্শী।
১৯৭১এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হতেই করিম নোয়াখালিতে তাদের গ্রামের বাড়িতে চলে যায়। সেখান থেকে সে আমাকে চিঠি লেখে। আমিও উত্তর দিই। এরকমই একটা চিঠিতে মনে পড়ে সে আমাকে তাসাদ্দুক নামক এক ‘সাচ্চা’ বিপ্লবী বা কমিউনিস্টের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ বা পরিচয়ের কথা জানিয়েছিল। ২৫ মার্চের ক্রাক-ডাউনের পর, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই আমি আবু করিমকে তার গ্রামের বাড়ির ঠিকানায় সাংকেতিক ভাষায় ইংরেজিতে একটি পোস্টকার্ড ছেড়েছিলাম। কোনোদিনই যা তার হাতে পৌঁছেনি। (সেদিন ইংরেজিতে ওই চিঠিটা লেখার পেছনে কোন্ বিবেচনা বা কী ধরনের নিরাপত্তা ভাবনা কাজ করেছিল আজ তা বলা মুশকিল।) মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য সীমান্ত অতিক্রমের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও আমি আমার সে-সময়ের সবচেয়ে প্রিয় এই বন্ধুটিকে ছেড়ে যেতে চাইনি। তাই তাকে চাটগাঁ আসতে বলে পরপর দু-তিনটি চিঠি দিয়েছিলাম। এর মধ্যে একটি চিঠি আমার বাবার মাধ্যমে করিমের বাবার হাতে পৌঁছে দিয়েছিলাম, যাতে বাড়ি যাওয়ার সময় তিনি সেটা নিয়ে যান। তাতে আমার পরিকল্পনা এবং ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগগুলোর কথা যতটা সম্ভব সাবধানতার সঙ্গে লেখা হয়েছিল। পরে জেনেছি সেটিও করিমের হাতে পৌঁছেনি। রাস্তায় চেকিংয়ের আশঙ্কায় তার বাবা সেটি ফেলে যান। ভাগ্যে তিনি সেটা নেননি, নিঃসন্দেহে আমি সেদিন নিরীহ ভদ্রলোকটিকে এক বিরাট ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিলাম। যাই হোক, আমার চিঠি না পেলেও করিম কিন্তু ঠিকই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে গিয়েছিল। পৌঁছেছিল আগরতলার সেই একই ঠিকানায় (ক্রাফ্ট হোস্টেল) যেখানে মাঝখানে অনেক ঘটনার পর আমিও গিয়ে উঠেছিলাম। তবে করিম সেখানে পৌঁছবার আগেই আমি ওখান থেকে চলে যাই। ফলে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। ন্যাপ-সিপিবি-ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ বাহিনীর হয়ে করিম সামরিক প্রশিক্ষণের জন্যও মনোনীত হয়েছিল। তবে তারা প্রশিক্ষণে রওনা হওয়ার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। দেশমুক্ত হওয়ার পর চাটগাঁ পৌঁছেই সে আমাদের বাসায় গিয়েছিল, আমি তখনও ফিরিনি। এ অবস্থায় আমার উদ্বেগাকুল মাকে (যিনি ইতিপূর্বে সীমান্তে আমার ধরা পড়ার সংবাদ ও নিহত হওয়ার গুজব শুনেছিলেন) সে বোধহয় আগরতলায় আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার বানানো গল্পও বলেছিল।
১৯৭২ সালে আমরা চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ক’ বন্ধু একসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হই। আবু করিম, মুস্তাফা, হুমায়ুন ও আমি বাংলা বিভাগে, মোহীত ও হারুন ইংরেজি বিভাগে। ততদিনে আবু করিমের কবিতা ও গল্প বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে প্রায় নিয়মিতভাবে ছাপা হচ্ছে। তার পরিচিতি ও যোগাযোগের বৃত্তটাও যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। আবার ঠিক এ সময়টাতেই খুব সম্ভব শামসুদ্দীন আহমদ (পেয়ারা), রায়হান ফিরদৌস মধু, আফতাবউদ্দীন আহমদ এঁদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং তাঁদের প্রভাবে সে জাসদ রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমি সে-সময় সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে সেভাবে আর যুক্ত না থাকলেও, কিছু কিছু বিষয়ে মতভিন্নতা ও ক্ষোভ নিয়েও, পুরনো দলের প্রতিই আমার আনুগত্য বজায় রেখে চলেছি। মনে আছে ১৯৭৩ সালের ডাকসু নির্বাচনের সময় আবু করিম জাসদ সমর্থক দৈনিক ‘গণকণ্ঠ’-এর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার, আর আমি দৈনিক সংবাদ-এর। তারপর ১৯৭৫ সালে আমরা যখন ‘যুবরাজ’ নামে একটি লিট্ল ম্যাগাজিন বের করলাম তখন চাটগাঁর আমাদের পুরনো বন্ধুদের সবাই আগেপরে কমবেশি সে-উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত হলেও, কেবল আবু করিমই এর বাইরে রয়ে যায়। হয়তো তার দিক থেকে এ ব্যাপারে আগ্রহের অভাব ছিল, কিংবা হতে পারে আমরা সেভাবে তাকে কাছে টানতে চেষ্টা করিনি। যদিও ‘যুবরাজ’-এর প্রতিটি সংখ্যায়ই আমরা তার লেখা খুব আগ্রহ করেই নিয়ে ছেপেছি। (প্রথম সংখ্যাতে সে নির্মলেন্দু গুণের ‘দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী’ বইটির একটি সুন্দর আলোচনা লিখেছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল তার গোটা চারেক চমৎকার কবিতা যথাক্রমে ‘দীপান্বিতা’ ও ‘কথামালা’ শিরোনামে।) মোটকথা কিভাবে যেন এ-সময় আবু করিমের সঙ্গে আমার এক ধরনের সূক্ষ্ম মানসিক দূরত্ব কিংবা, আরও সঠিকভাবে বললে, বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে অদৃশ্য টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়। রাজনীতি এর একটা কারণ হতে পারে, তবে তাকে মুখ্য বা এমনকি একটা বড় কারণ হিসেবে মানতে আমি কখনোই রাজি হব না। কারণ আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীতে সে-সময় বা বলতে গেলে সকল সময়ই সব দলমতের সুন্দর সহাবস্থান ছিল। পরে আবু করিম যখন আরও সক্রিয়ভাবে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে রাজনীতিতে জড়িত হয় তখনও কিন্তু রাজনৈতিক মতভিন্নতা আমাদের পুরনো ঘনিষ্ঠতাকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।
ইদানীংকার কথা জানি না, তবে আমাদের কৈশোর ও তারুণ্যের দিনগুলোর কথা স্মরণ করলে, আবু করিমের চরিত্রের যে-বৈশিষ্ট্যটির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে তা হল তার মুগ্ধতাবোধ। খুব সহজেই যে-কেউ বা যে-কোনো কিছু তাকে মুগ্ধ করতে পারত। আর কেবল নিজে মুগ্ধ হয়েই সে ক্ষান্ত হত না, অন্যদের মধ্যেও সে-মুগ্ধতা সঞ্চারের একটা প্রবল তাগিদ যেন নিজের মধ্যে অনুভব করত। এভাবে সৈয়দ শামসুল হক বা আল মাহমুদের কোনো কবিতাগ্রন্থ পাঠের মুগ্ধতা নিয়ে সে হয়তো কিছুদিন ক্লান্তিহীনভাবে আমাদেরকে বুঝিয়ে চলল, কেন ওই কবিদের অনতিবিলম্বে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত। কিংবা হয়তো ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সেখানকার বাজারের চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে দিতেই সে কোনো দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে আবিষ্কার করে ফেলল, তারপর সে- বিপ্লবীর গুণগান করে আমাকে দীর্ঘ চিঠি। হয়তো কমলাপুর রেল স্টেশনে টিকেট কাটতে গিয়ে তার সঙ্গে ফোর্থ ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত কোনো মস্ত ইতালিয়ান ট্রটস্কাইটের পরিচয় হয়ে যায়। তারপর আমাদের অবিশ্বাসকে কিছুমাত্র পাত্তা না দিয়ে কযেকদিন ধরে চলে তার সে গল্প। এমনি সব মজার মজার ঘটনা! আজ বুঝি যে, সহজে মুগ্ধ হতে পারার ক্ষমতা, এ-ও মানুষের এক বড় গুণ। আর এই মুগ্ধতাবোধ ছাড়া আর যাই হোক কবি বা শিল্পী হওয়া যায় না । সেদিন কিন্তু আবু করিমের এই মুগ্ধতা নিয়ে আমরা মোটের ওপর মজাই করেছি। তারপরও এভাবে আবু করিমের মুখে শুনে শুনেই তো অন্তত আমার অনেক ভালো বই পড়া হয়েছে। এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি. ফতেহ্ লোহানীর চমৎকার অনুবাদে হেমিংওয়ের ‘ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দ্যা সি’ উপন্যাসটি (‘সমুদ্র সম্ভোগ’ নামে) এবং সৈয়দ শামসুল হকের ‘রক্ত গোলাপ’ ও ‘আনন্দের মৃত্যু’ বই দুটি আমি পড়ি প্রধানত করিমের উৎসাহেই। তার আগ্রহাতিশয্যেই অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় ও পরে বন্ধুত্ব হয়েছে। এমনি একজন হারুন শফিউদ্দীন। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ, মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল (আবু করিমও বোধহয় আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবে) এই বন্ধুটি (বর্তমানে প্রবাসী) এক সময় চমৎকার কিছু গল্প লিখেছে, ভালো ছবি আঁকতে পারত (এখন কি আর লেখে, আঁকে? জানি না), মুখে মুখে সুন্দর গল্প ও জোক বলতে পারত, তার বাংলা ও ইংরেজি উভয় হাতের লেখাই ছিল ভারি সুন্দর, ছাত্র হিসেবেও সে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। তো তার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয়ের আগেই আবু করিম চাটগাঁ কলেজের তার এই হোস্টেল-মেটটিকে আমার কাছে এক বিস্ময়-বালক হিসেবে উপস্থাপন করে। আরও মজার ব্যাপার হল, পরবর্তীকালে হারুনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হওয়ার পর জানতে পারি, একইভাবে হারুনের কাছে আমার গুরুত্ব বাড়াতে সে আমার ওপরও নানা অন্যায্য গুণ আরোপ করে তার কাছে তুলে ধরেছিল।
চট্টগ্রামে আমাদের সে গভীর বন্ধুত্বের দিনগুলোতে আমরা কথা বলতে বলতে মাইলের পর মাইল হেঁটেছি। একসঙ্গে রিক্সায় আমরা কবার চড়েছি, কিংবা আদৌ কখনো চড়েছি কি না, আজ মনে করা কঠিন। যাতায়াতের পথে রাস্তার ধারের বা কাছাকাছি সবকটি বুকস্টলে ও পুরনো বইয়ের দোকানে একবার হানা দেওয়া ছিল আমাদের রোজকার অভ্যাস। অনেক সময় আবার একই স্টলে যেতে-আসতে দুবারও। বইপত্র যে আমরা খুব একটা কিনতাম তা নয়। সে সামর্থ্যও আমাদের দুজনের কারো ছিল না। তবে এভাবে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে অনেক দোকানের মালিক বা কর্মচারীদের সঙ্গেই আমাদের আলাপ বা মুখচেনা রকমের পরিচয় হয়ে যায়। যেচে আলাপ জমানোর ব্যাপারে আবু করিমের একটা অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। তো যা বলছিলাম, যাওয়া-আসার পথে স্টলে দাঁড়িয়েই করিম অনেক সময় তার আগ্রহের কোনো বই বা পত্রিকা পড়ে শেষ করে ফেলত। তার সঙ্গী হিসেবে আমি সঙ্কোচ বোধ করতাম, বিরক্ত হতাম। কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপহীন। ‘এই একটু, আর একটু’ করে সে পড়েই চলত।
আবু করিমকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি, অনেক বলবার কথা। অন্তত আমার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল, পবিত্র ও মহৎ দিনগুলোর অনেকটাই জুড়ে ছিল সে। বর্তমান লেখার পরিসরে বলা বাহুল্য যার খুব সামান্যই উল্লেখ করা সম্ভব । বাকিটা ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন স্মৃতিকথা লিখি, অর্থাৎ ঈশ্বর আমাকে সে তওফিক দেন, তার জন্য তোলা রইল।
আমাদের সে মাখোমাখো বন্ধুত্বের দিনগুলোতে একটা কথা আমরা, মানে আমি আর আবু করিম, প্রায়ই বলতাম, ‘আমাদের কোনো গন্তব্য নেই, চলাই আমাদের লক্ষ্য।’ কথাটা কার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে প্রথম বেরিয়েছিল কিংবা আমাদের মধ্যে কে তা প্রথম উচ্চারণ করেছিলাম আজ আর মনে করতে পারছি না। তবে, চালিয়াতি কথা দিয়ে চমক সৃষ্টির জন্য নয়, সেদিন সত্যিসত্যি বিশ্বাস করেই আমরা কথাটা বলতাম। হ্যাঁ, আমাদের বয়সটা সেদিন তার পক্ষে অনুকূল ছিল। কিন্তু সেটাও বোধ হয় সবকথা নয়। মোটামুটি সত্তর দশক পর্যন্ত আমাদের সবার জন্যই সে এক অন্যরকম সময় ছিল। বিশ্বাস করবার সময়; বিশ্বাসের জন্য একেবারে জান লড়িয়ে দিতে না পারি, কথায় ও কাজে সত্য হবার অন্তত দায়টুকু আমরা সেদিন অনেকেই অনুভব করতাম। আজ সে জায়গা থেকে আমরা সবাই কমবেশি সরে এসেছি। নাকি বলব সময় আমাদের সরিয়ে এনেছে? হতে পারে, তর্ক করব না! বয়স ও জীবনযাপন প্রণালী এর মধ্যে আমাদের অনেকের দেহে এবং সেই সঙ্গে মস্তিষ্কেও কমবেশি চর্বির সঞ্চার করেছে। এই বয়সে সত্যিকার সৃজনশীল থাকা বাস্তবেই কঠিন। সত্যি কথা বলতে কী, অনেকের বেলায় পুরনোর অনুবর্তনকেই আমরা সৃষ্টিশীলতা বলে ভুল করি। সেদিক থেকে আবু করিম আজও আমার ঈর্ষা জাগায়।
আবু করিমের প্রথম দিকের প্রায় সব কবিতার ও অধিকাংশ গল্পের বলতে গেলে আমিই প্রথম পাঠক বা শ্রোতা। সেই থেকে তিন দশক পর আজও তার কবিতার আমি অত্যন্ত মুগ্ধ পাঠক। তার ‘কবিতাসমগ্রে’র পৃষ্ঠা ওল্টাতে গিয়ে অনেক কবিতাকেই আমার ভীষণ চেনা-চেনা লাগে । মনে হয় যেন এগুলো আমারই লেখা! অথবা আমি লিখতে চেয়েছিলাম, পারিনি। যোগ্যতার কথা বাদ দিলেও, এ ধরনের মুগ্ধতা নিয়ে বলা বাহুল্য তার কবিতার যথার্থ আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে আমি সে চেষ্টা করবও না। আজ শুধু একটা কথা আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এতকাল পর তার ঠিক মনে আছে কি না জানি না, কৈশোরের সেই দিনগুলোতে আমরা মাঝে মাঝে ভাবতাম, আহা, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ‘কাজলা দিদি’র মতো মাত্র একটি কবিতা যদি লিখতে পারতাম! ‘কাজলা দিদি’র চেয়ে শিল্পমানে অনেক-অনেক ভালো কবিতা আবু করিম এর মধ্যে লিখেছে, তার কিছু কবিতা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবার যোগ্য বলেও আমি মনে করি। কিন্তু ‘কাজলা দিদি’র মতো একটি কবিতা কি সে এ-পর্যন্ত লিখতে পেরেছে? যদি না পেরে থাকে, তবে তার আত্মতৃপ্তির বা কলমকে বিশ্রাম দেবার সুযোগ কোথায়? মানুষকে তো তার স্বপ্ন বা অঙ্গীকার দিয়েই মাপতে একদিন আমরা শিখেছিলাম।
আবু করিমের বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। কামনা করব, আমার আয়ু নিয়ে হলেও, আমার এই প্রতিভাবান প্রিয়-পুরাতন বন্ধুটি সৃজনক্ষম শতবর্ষ পার করুক। আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীতে আবু করিমের মতো কিংবা হয়তো তার চেয়েও প্রতিভাবান আরও কেউ কেউ ছিলেন। কিন্তু জীবনের কঠিন বাস্তবতা কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রতিষ্ঠার মোহন হাতছানি তাঁদেরকে আজ অন্য বৃত্তে টেনে নিয়ে গেছে (কামনা করি, তাঁরাও তাঁদের নির্বাচিত জীবনে সফল ও সুখী হোন)। স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রতিষ্ঠার মুখ ইতোমধ্যে করিমও দেখেছে। তবে সৃষ্টিশীল জীবনের অনিবার্য দুঃখকে সে এজন্য পরিত্যাগ করেনি। আগামী দিনগুলোর জন্য আশা করব, অপ্রাপ্তির ক্ষোভ কিংবা সহজ খ্যাতি বা স্বীকৃতির মোহ যেন তাকে বিচলিত না করে। এমনকি যুগের বিকার থেকেও তাঁর প্রতিভাই যেন তাকে অনাক্রম্যতা দেয়। হ্যাঁ, তার চেয়ে অনেক কম প্রতিভার অধিকারী কেউ কেউও হয়তো পদ, প্রতিষ্ঠান, বিত্ত ও যোগাযোগ কৌশলের গুণে এর মধ্যে লেখক হিসেবে অধিক পরিচিতি, প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার-স্বীকৃতি ইত্যাদির অধিকারী হয়েছে। সবদেশে সবকালেই এমনটি ঘটে থাকে। তারপরও এ নিয়ে একজনের মনে কমবেশি দুঃখ বা অভিমান থাকতেই পারে। করিমের আজকের পেশাগত বা সামাজিক অবস্থানে উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলো তার পক্ষেও হয়তো অনধিগম্য নয়। তবু, তবু আশা করব, তার প্রতিভায় গভীর আস্থা আছে বলেই আশা করব, বঞ্চনাবোধ বা খ্যাতি-যশের মোহ থেকে সে যেন নিতান্ত সহজের পথে পা না বাড়ায়। চারপাশে প্রতিভাহীনদের পরাক্রম দেখে সে যেন হতাশ, বিভ্রান্ত না হয়। জানি আজকের এই বিজ্ঞাপন ও মিডিয়া-দৌরাত্মের যুগে এ প্রত্যাশার মধ্যে একটা নির্বুদ্ধিতার ব্যাপার আছে। তবে নির্বোধের আশাও তো আশাই! কাজেই আশা করতে দোষ কী?
আমাদের বন্ধুত্বের প্রথম দিনগুলোতে শামসুর রাহমানের অনুবাদে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা পড়ার সুযোগও আমার হয়েছিল সম্ভবত আবু করিমের কল্যাণেই। আজ তার পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রস্টের সেই বিখ্যাত পংক্তিটি উদ্ধৃত করেই আমার এ-লেখাটি শেষ করতে চাই : ‘যেতে হবে বহুদূর ঘুমিয়ে পড়ার আগে।’
…….
২০০৩
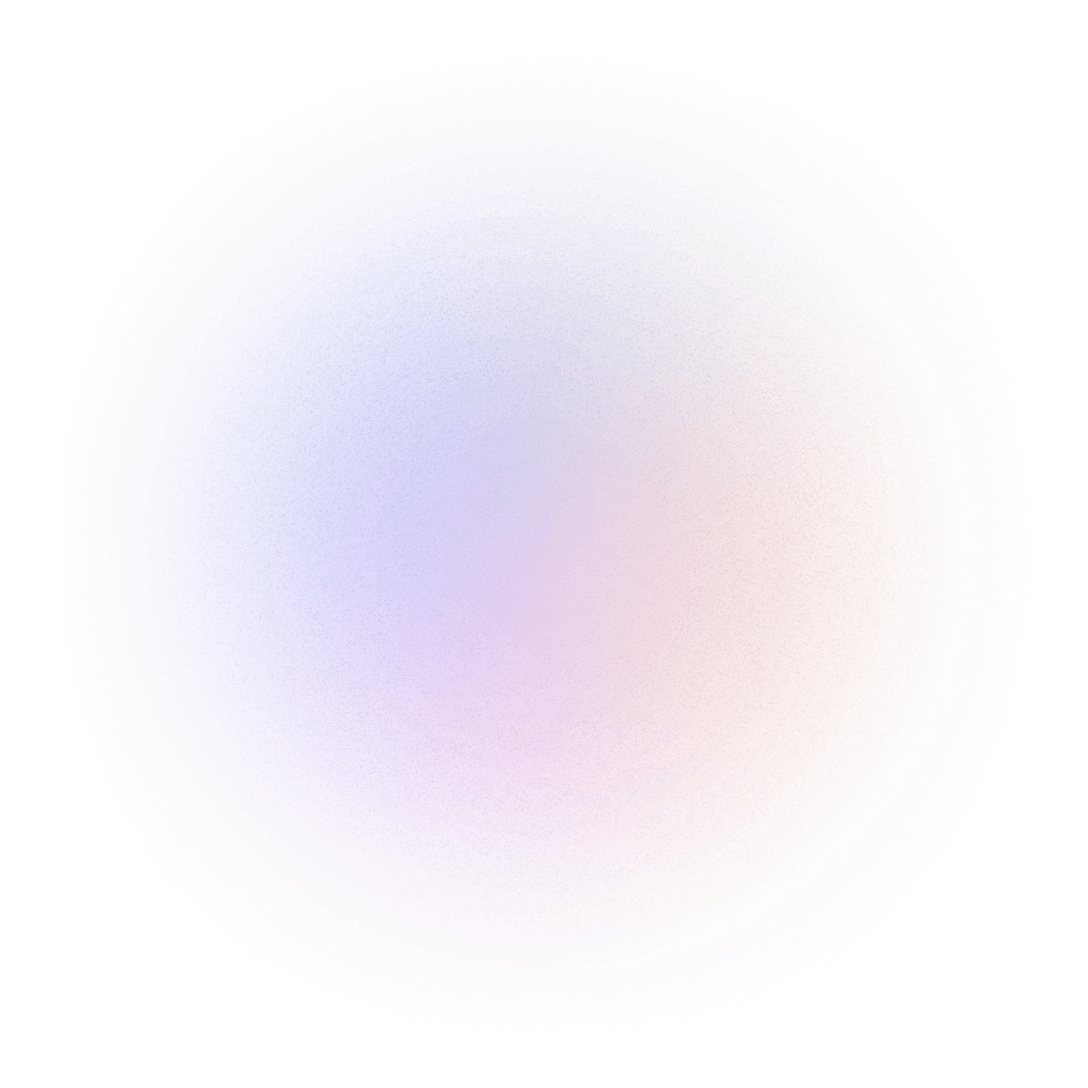
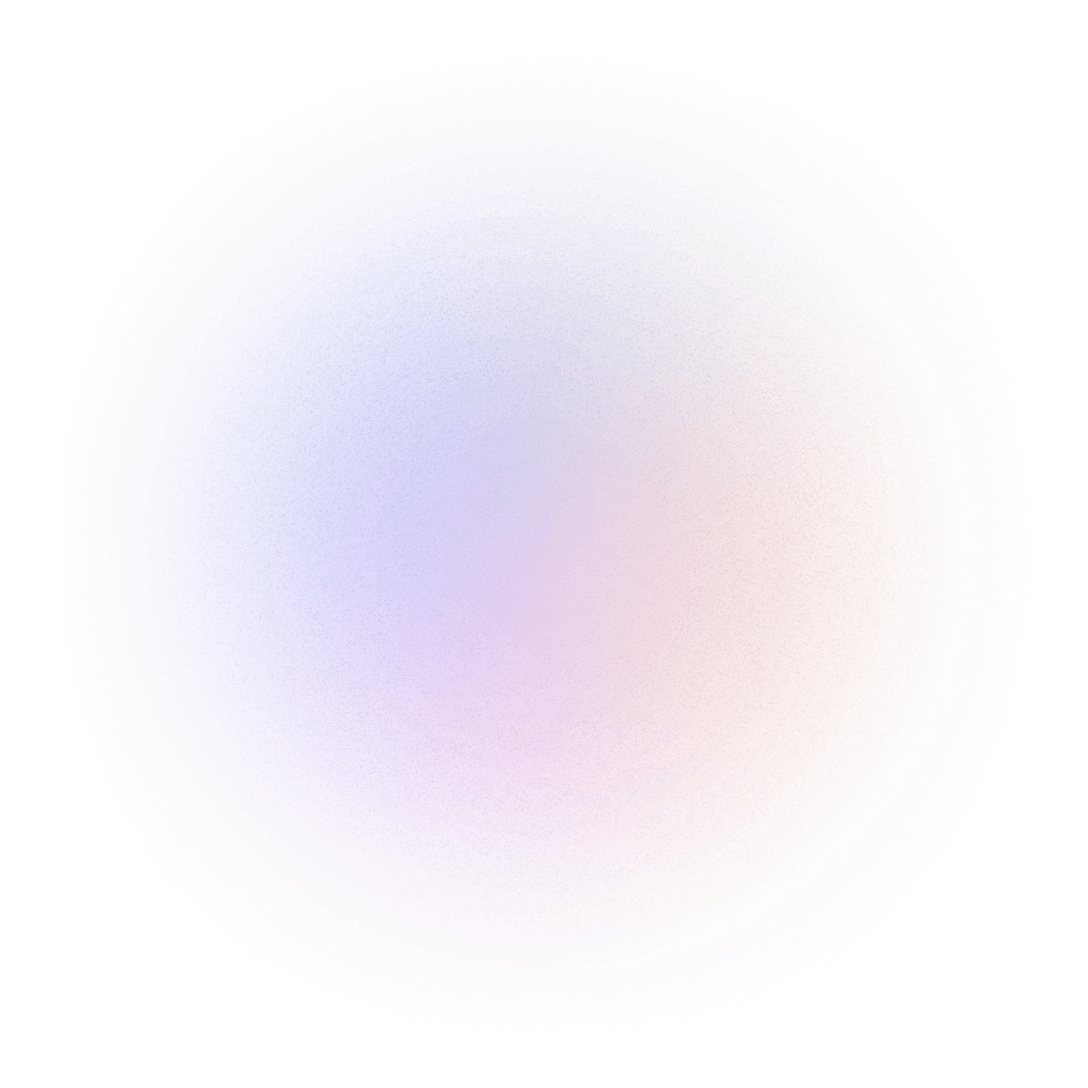

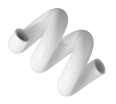
Leave a Comment